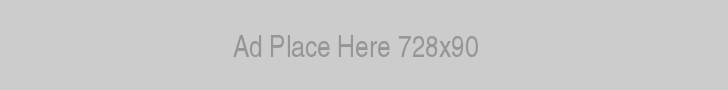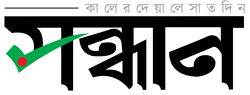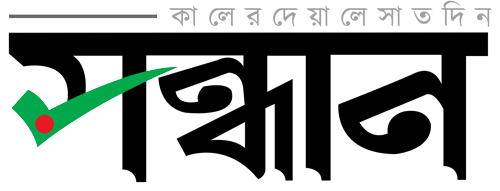ড. আর এম দেবনাথ : গত ৯ জুন যথানিয়মে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট ঘোষিত হয়েছে। এরপর বাজেটের ওপর অর্থমন্ত্রী মহোদয় সংবাদ সম্মেলন করেছেন।
অর্থনীতিবিদ, গবেষক, ব্যবসায়ী ও বিশ্লেষকরা যার যার মতো করে বক্তব্য দিয়েছেন। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে প্রাধান্য পাচ্ছে-পাচারকৃত টাকা দেশে ফেরত আনা, মূল্যস্ফীতি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মধ্যবিত্তের পাওনা-দেনা।
কোনটা রেখে কোনটার ওপর আলোচনা করি, তা ঠিক করা একটি কঠিন বিষয়। তবে বেশি আলোচিত হচ্ছে পাচারকৃত টাকা দেশে ফেরত আনার বিষয়টি। কিন্তু এর ওপর আলোকপাত করা একটু কঠিন। কারণ অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলছেন এক কথা, আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর বলছেন অন্য কথা।
অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল সামান্য ট্যাক্সে পাচারকৃত অর্থ দেশে আনতে চান। তিনি এও বলেছেন, এটি করলে কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। এই হচ্ছে মন্ত্রী মহোদয়ের কথার মূল বক্তব্য। কিন্তু গভর্নর সাহেবকে বিশ্বাস করলে বলতে হয়, যার কোনো অস্তিত্ব নেই তা তিনি কীভাবে দেশে আনবেন? গভর্নর বলছেন, তাদের হিসাবে বিদেশি ব্যাংকে বাংলাদেশিদের কোনো পাচারকৃত টাকা নেই।
যা আছে তা বাংলাদেশিদের বিদেশে অর্জিত টাকা, পাচারকৃত নয়। আর আছে আমদানি-রপ্তানি বিলের সেটেলমেন্টের অপেক্ষারত টাকা। এখন গভর্নর সাহেবের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে পাচারকৃত টাকা কোথায়? অবশ্য অর্থমন্ত্রী মহোদয় বলছেন, খেলাপিদের মধ্যে অনেকেই যারা টাকা পাচার করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
তাই তার আশা, টাকা ফেরত আসবে। প্রশ্নের মুখে তিনি সবাইকে বলেছেন, এই উদ্যোগে বাধা না দিতে। যারা বাধা দিচ্ছেন, তারা বাধা দিচ্ছেন আইনের কথা উল্লেখ করে আর নৈতিকতার কথা বলে। বলছেন, এতে কালো টাকার মালিকরা উৎসাহিত হবে।
পক্ষে-বিপক্ষের বক্তব্যে না গিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করা যায়। বিদেশে পাচারকৃত টাকা পাচারকারীরা কি ব্যাংকের মাধ্যমে ডলার হিসাবে আনবেন, না হুন্ডির মাধ্যমে টাকায় আসবে? আবার পিকে হালদারের মতো যাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা আছে, তারাও কি এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে? ইত্যাকার অনেক প্রশ্ন। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, পাচারকৃত টাকা আদৌ আসবে কিনা?
অর্থমন্ত্রী মহোদয় অনেক দেশের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি আশাবাদী। অবশ্য অর্থমন্ত্রী মহোদয় একটি বিকল্প ব্যবস্থার দিকেও যেতে পারতেন। জাতিসংঘ কনভেনশনের পথ ধরে সরকার বাংলাদেশিদের সব বিদেশি সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারত এবং জাতীয়করণ করতে পারত। তা করে জাতিসংঘকে বলতে পারত এসব টাকা উদ্ধার করে দিতে। শুনেছি এ পথেও অনেক দেশ পাচারকৃত টাকা দেশে আনতে পেরেছে।
স্পষ্টতই সরকার ওই পথে যায়নি। দেখা যাক বছর শেষে দেশে কত ডলার ফেরত আসে। এদিকে বিদেশ থেকে যত ইচ্ছা ডলার নিয়ে যে কেউ দেশে আসতে পারবে। কোনো প্রশ্ন, কাগজপত্র চাওয়া হবে না। বোঝাই যায়, সরকার জরুরি ভিত্তিতে ডলার চায়, কারণ ডলারের রিজার্ভ হ্রাস পেলে ভীষণ বিপদে পড়বে বাংলাদেশ। এই বিপদ থেকে মুক্তির আগাম চিন্তা এগুলো। এখন ফলাফলের অপেক্ষা।
দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনায় আসছে তা হচ্ছে ‘মূল্যস্ফীতি’ (ইনফ্লেশন)। মূল্যস্ফীতি এখন সরকারি হিসাবেই ৭ শতাংশের কাছাকাছি। ভরা বোরো মৌসুম। অথচ এখন চালের দাম বাড়ছে। আটা-ময়দা, রুটির দাম বাজারে বেড়েছে। এর সঙ্গে জড়িত ভর্তুকির বিষয়টি। জ্বালানি তেল, সার, কয়লা, সয়াবিন, গম ও ভুট্টা নিয়ে সরকার উদ্বিগ্ন।
কারণ এগুলোর দাম বর্তমান স্তর থেকে আরও বেশি বাড়লে ভর্তুকি দিতে হবে ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। এমনিতেই ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভর্তুকির পরিমাণ ৫৩ হাজার ৮৫২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৬ হাজার ৮২৫ কোটি টাকা। বর্তমান হিসাবে আগামী বছরে তা হবে ৮২ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা।
এর পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। এই টাকার বাড়ি কোথায়? ভর্তুকি না বাড়ালে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে হু হু করে। আর জ্বালানি তেল, গ্যাস, কয়লা, গম, ভুট্টার দাম বাড়লে বাজারে আগুন লাগবে। আবার ভর্তুকি বাড়ালে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ বাড়বে মারাত্মকভাবে। ঘাটতি বাড়লে তা মেটানোর ব্যবস্থা হবে অভ্যন্তরীণভাবে ঋণগ্রহণ। আর সেটা হবে ব্যাংক ঋণ।
২০২২-২৩ অর্থবছরে যে প্রাক্কলন করা হয়েছে, তাতে ঘাটতি মোট ২ লাখ ৪৫ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৯৮ হাজার ৭২৯ কোটি টাকা আসবে বিদেশি ঋণ হিসাবে, আর দেশি ঋণ হচ্ছে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা। ৩৫ হাজার কোটি টাকা হচ্ছে যাতায়াতের ঋণ। বাকিটা ব্যাংক ঋণ। এত পরিমাণ ব্যাংক ঋণ সরকার নিলে বেসরকারি খাতের ঋণে টান পড়বে বলে ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এখন যদি ঘাটতি আরও বাড়ে, তাহলে তার সংস্থান কোত্থেকে হবে? এখনই বাজারে তারল্য সংকট। আর ঘাটতি বাড়লে সংকট মহাসংকটে পরিণত হতে পারে।
এসব বিবেচনা করে সরকার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় একটা বের করেছে। সরকার ‘চাহিদা প্রবৃদ্ধির’ হার কমাবে এবং বিপরীতে সরবরাহ বাড়বে। এ দুটি কাজই কঠিন। চাহিদা কমানোর জন্য সরকারি ব্যয় আগের মতো বাড়ানো হয়নি। কারণ সরকারি ব্যয় যত বেশি, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তত বেশি। এ কারণে বাজেটের আকার আগামী বছরের জন্য সেভাবে বাড়ানো হয়নি।
এতে বহু খাত আগের মতো বেশি বেশি বরাদ্দ পায়নি, এমনকি সামাজিক নিরাপত্তা খাতও। আবার সরবরাহ বৃদ্ধিতেও সমস্যা। জ্বালানি তেল, গম-ভুট্টার সরবরাহ বাড়ানোর বিষয়টি নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাজারে এসবের প্রাপ্যতার ওপর। দেখা যাচ্ছে, ইউক্রেন যুদ্ধে গম-ভুট্টার সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে রয়েছে। অতএব সরবরাহ বাড়ানোর সম্ভাবনা নানাভাবে বিঘ্নিত। এদিকে রয়েছে চালের প্রশ্ন। তাও লাগবে।
বড় কথা হচ্ছে, চাহিদা সরকার কীভাবে কমাবে। ধনী ব্যক্তিদের চাহিদায় কিছুটা লাগাম টানা সম্ভব। প্রসাধনী সামগ্রী, ফলমূল, টেলিভিশন-ফ্রিজ, গাড়ি ইত্যাদির চাহিদা কিছুটা কমানো সম্ভব। কিন্তু সমস্যা গরিব-নিম্নবিত্তদের নিয়ে। তাদের জীবন-জীবিকায় ভোগ্যপণ্য, শাকসবজি, চাল, ডাল, নুন, তেল, পেঁয়াজ, রসুনের চাহিদা বেশি। এগুলোর চাহিদা কমানো কি সম্ভব? কীভাবে চাল-গমের চাহিদা এ ক্ষেত্রে কমানো যাবে?
এটা অসম্ভব বিষয়। অথচ দেশের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ মানুষই এ পর্যায়ে পড়ে। এ অবস্থায় চাহিদা/ভোগ সরকার কীভাবে কমাবে, তা প্রশ্নাতীত নয়। এ ক্ষেত্রে জিনিসপত্রের মূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে হলে দুটি কাজ করা যেতে পারে। প্রথমত, সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট ইত্যাদি হ্রাস করতে পারে। কিন্তু এর জন্য বিপরীতে ধনীদের কর বাড়াতে হবে।
দৃশ্যত সরকার এ পথে হাঁটতে চায় না, যে কারণে দেখা যাচ্ছে সরকার পরপর তিন বছর করপোরেট কর হ্রাস করেছে। বস্তুত ব্যবসায়ীরা যা চাইছে, বিশেষ করে খেলাপি গোছের ব্যবসায়ীরা যা চাইছে, সরকার তা-ই করছে। এ অবস্থায় ধনীদের ওপর করারোপ করা সুকঠিন বিষয়। তাহলে মানুষের কর্মসংস্থান করতে হয়। কমসংস্থানের একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বর্তমান অর্থমন্ত্রী মহোদয় ঋণের ওপর সুদের হার ‘সিঙ্গেল ডিজিটে’ নামিয়েছেন। ফলে হ্রাস পেয়েছে আমানতের ওপর সুদহার। কথা ছিল ৯-৬ শতাংশের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ব্যাংকগুলোর মধ্যে খুব কমই আমানতে ৬ শতাংশের সুদ দেয়। বর্তমান সুদের হার মূল্যস্ফীতির হারের চেয়েও কম। বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশ দিয়েছিল আমানতের ওপর সুদের হার মূল্যস্ফীতির উপর রাখতে।
কে কার কথা রাখে! ফলে আমানতের বাজার মন্দা। এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ‘রেপো’ রেট (যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেয়) বাড়িয়েছে। এর ফলে ঋণের ওপর সুদের হার বাড়ার কথা। এটি হলে কি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আমানতের ওপর সুদের হার বাড়াবে? আবার রয়েছে সঞ্চয়পত্র। সুদ পরিশোধে অনেক টাকা যাচ্ছে বলে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানো হয়েছে। সঞ্চয়পত্র বিক্রির ওপর নানা বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে।
অথচ দেখা যাচ্ছে, মোট বাজেট বরাদ্দে সুদ বাবদ খরচের পরিমাণ শতাংশের হিসাবে হ্রাস পাচ্ছে। অথচ এর ওপর সুদের হার আরও কমানোর অব্যাহত চাপ রয়েছে। আবার দেখা যাচ্ছে, এসব কারণে বেসরকারি বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে এক দশক ধরে। বরং বহু ব্যবসায়ী-শিল্পপতি দেশে বিনিয়োগ না করে বিদেশে টাকা পাচার করে দিচ্ছে, যার স্বীকৃতি সরকার এবারের বাজেট দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট-উত্তর সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, ‘আমি তো বলিনি টাকা পাচার হচ্ছে না।’ এসব থেকে কী মনে হয়? বিনিয়োগ বাড়বে, কর্মসংস্থান হবে? খুবই সন্দেহজনক বিষয়। যা কর্মসংস্থান আছে তাতেও সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।
কোভিড-পরবর্তীকালে অর্থনীতি মোটামুটি ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধ আবার পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। বাজারে জিনিসের দাম বাড়ছে, ডলারের সংকট তৈরি হচ্ছে, জাহাজের ভাড়া বাড়ছে। এ অবস্থায় কয়জন বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াবে, তা দেখার বিষয়। এমনকি কয়জন বর্তমানে কর্মরত মানুষদের চাকরিতে রাখে, তাও দেখতে হবে। আবার রয়েছে ‘রোবট’ বসানোর প্রবণতা। অতএব কর্মসংস্থান অনিশ্চিত। তাহলে উপায়? উপায় সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বাড়ানো, ভাতা ইত্যাদির পরিমাণ বাড়ানো।
কিন্তু হিসাবে দেখা যাচ্ছে, জিডিপির অনুপাতে সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে। অনেক ভাতার পরিমাণ গত ছয় বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়ে যাচ্ছে। আবার সামাজিক সুরক্ষায় এমন খাতও ঢুকছে, যা সামাজিক সুরক্ষা নয়। যেমন ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির টাকা, অবসরপ্রাপ্তদের অবসর ভাতা, সঞ্চয়পত্রের সুদ ইত্যাদি। এসব খাতের টাকা বাদ দিলে দেখা যাচ্ছে, সামাজিক সুরক্ষার বরাদ্দ বরং হ্রাস পাচ্ছে।
অথচ গরিব মানুষকে, অতিগরিব মানুষকে বাঁচানোর আর কোনো পথ, বিকল্প পথ নেই। সস্তায় খাবার, খাদ্য সরবরাহ, বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ, নগদ টাকা প্রদান, তেল-ডাল-পেঁয়াজ প্রদান ইত্যাদিতে প্রচুর টাকা সরবরাহ করা দরকার। কিন্তু এর সার্বিক আয়োজন কমই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।
এদিকে রয়েছে মধ্যবিত্তের বিষয়, যা এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। অর্থমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, দেশে ৪ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত, তারা কর দিতে পারে অথচ অনেকেই দেয় না। এই চার কোটি মানুষ সংখ্যায় কম নয়। প্রশ্ন, ২০২২-২৩ বাজেটে তাদের কী দেওয়া হয়েছে? শূন্য বললে কম বলা হয়। মধ্যবিত্ত কর দেয়। তার করের হার, করমুক্ত আয়সীমা কোনোটাই কমানো হয়নি। কয়েক বছর পরও তা একই আছে।
অথচ প্রতিবছর ৫-৬ শতাংশ হারে মূল্যস্ফীতি ঘটে চলেছে। এর বিপরীতে তাদের কিছুই দেওয়া হলো না। বরং উলটো বিনিয়োগের পরিমাণ কমানো হয়েছে। আগে মোট আয়ের ২৫ শতাংশ বিনিয়োগ করলে রেয়াত পাওয়া যেত। এখন তা ২০ শতাংশ। ৩৮ ধরনের সেবায় ‘কর রিটার্ন’ দেখানোর বাধ্যবাধকতা চালু হবে। এতে মধ্যবিত্তের হয়রানি বাড়বে। অথচ তারা হাত পাততে পারে না। এ কথাটি কেউ বিবেচনা করে না।
ড. আর এম দেবনাথ : অর্থনীতি বিশ্লেষক; সাবেক শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়