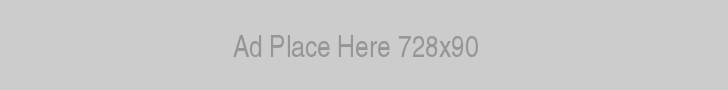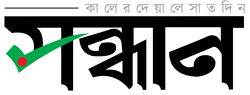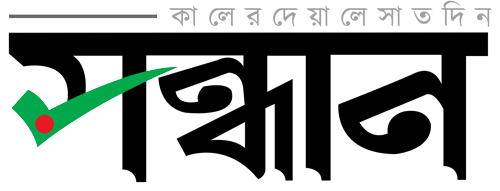প্রবল চাপে পড়েছে জাতীয় সঞ্চয়। সব খাতেই মানুষের সঞ্চয়ের প্রবণতা কমে যাচ্ছে। এতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সঞ্চয়ের প্রবৃদ্ধিতে। অব্যাহত গতিতে সঞ্চয় কমার কারণে ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে।
সরকার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে নীতিমালা কঠোর করায় ও মানুষের সক্ষমতার অভাবে এর বিক্রি অর্ধেকে নেমে গেছে। পণ্য ও সেবার মূল্যে লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি ও মানুষের আয় কমায় সঞ্চয় করার প্রবণতা কমে গেছে। এছাড়া চড়া মূল্যস্ফীতির কারণে ব্যাংকে টাকা রাখলে তা বাড়ার চেয়ে বরং কমে যাচ্ছে।
দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন, অব্যাহতভাবে সঞ্চয় কমে যাওয়ার প্রবণতা ভালো লক্ষণ নয়। সঞ্চয় না বাড়লে ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঋণের জোগান দেওয়া কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এতে বাধাগ্রস্ত হবে অর্থনীতির বিকাশ। যা দেশের মানুষের আয় কমিয়ে দেবে। নতুন কর্মসংস্থান বাড়ার গতি থমকে যাবে। চাকরিচ্যুতির সংখ্যা বেড়ে যাবে। এসব বিবেচনায় নিয়ে সরকারকে এখনই সতর্ক হতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে সংকট আরও প্রকট হবে।
এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সঞ্চয় কমার অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে পণ্যমূল্য বেড়ে যাওয়া। এ কারণে মানুষের খরচ বেড়েছে। অন্যদিকে করোনার পর অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম পুরোপুরি না হওয়া ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ায় মানুষের আয় না বেড়ে বরং আরও কমেছে।
এতে মানুষ এখন নিত্যদিনের খরচ মিটিয়ে নগদ টাকা জমা রাখতে পারছেন কম। ফলে ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে সঞ্চয় কমছে। এতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নতুন তারল্যের জোগান কমে গেছে। এটি এখনও প্রকট আকার ধারণ করেনি। তবে এভাবে চলতে থাকলে এক সময় প্রকট আকার ধারণ করবে বলে তারা সতর্ক করেছেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, মোট জাতীয় সঞ্চয়ের মধ্যে ৭০ শতাংশ আসে ব্যাংক খাত থেকে। বাকি ৩০ শতাংশ জাতীয় সঞ্চয়পত্র, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে।
ব্যাংকিং খাতে মে পর্র্যন্ত গ্রাহকদের আমানতের স্থিতি ১৪ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মেয়াদি বা কিস্তি ভিত্তি সঞ্চয় প্রকল্পে আমানত ১২ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। চলতি আমানত ১ লাখ ৭০ হাজার কোটি টাকা। চলতি আমানত যে কোনো সময় গ্রাহক তুলে নিতে পারেন। কিন্তু মেয়াদি আমানত সাধারণত গ্রাহকরা জরুরি প্রয়োজন ছাড়া তোলেন না। আর তুলে নিলেও মুনাফা খুবই কম দেওয়া হয়। সঞ্চয়কারীরা মূলত মেয়াদি আমানতের হিসাবেই সঞ্চয় করেন। আর মেয়াদি সঞ্চয় দিয়েই ব্যাংকগুলো শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণ করে। ব্যাংক খাতে সার্বিক আমানত কমার পাশাপাশি মেয়াদি আমানতও কমতে শুরু করেছে। মোট আমানতের ৮০ শতাংশই মেয়াদি আমানত। বাকি ২০ শতাংশ চলতি আমানত। ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-মে মাসে মোট আমানত বেড়েছিল ৫৫ শতাংশ। সদ্য বিদায়ি অর্থবছরের একই সময়ে মোট আমানতের প্রবৃদ্ধি তো বাড়েইনি। উলটো কমেছে ৪০ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরের আলোচ্য সময়ে চলতি আমানত বেড়েছিল ৩০২ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ে বাড়ার পরিবর্তে কমেছে ৭৯ শতাংশ। মেয়াদি আমানত ২০২০-২১ অর্থবছরে বেড়েছিল ৪৪ শতাংশ। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরের একই সময়ে বাড়ার পরিবর্তে কমেছে ৩৫ শতাংশ।
এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একজন গবেষক বলেন, করোনার সময়ে অর্থনীতিতে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে এখনও পরিত্রাণ পাওয়া যায়নি। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে একটু সময় লাগবে। তবে আমানতের প্রবৃদ্ধির হার কমার গতি হ্রাস পেয়েছে। ৩ মাস আগেও আমানতের প্রবৃদ্ধি কমেছিল ৬০ শতাংশ। এখন তা কমে ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে। বর্তমানে বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমানতের প্রবৃদ্ধির গতি হয়তো আরও একটু কমতে পারে। তবে তা ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে বলে আশা করেন ওই কর্মকর্তা।
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমানতের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক। অর্থাৎ আগের চেয়ে আমানত কমছে। গত বছরের মার্চে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমানতের স্থিতি ছিল ৪৩ হাজার কোটি টাকা। চলতি বছরের একই সময়ে তা ৪২ হাজার কোটি টাকায় নেমে এসেছে। আলোচ্য এক বছরের ব্যবধানে আমানত কমেছে ১ হাজার কোটি টাকা। আমানত কমেছে প্রায় আড়াই শতাংশ।
এ খাতে দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাবে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান সংকটে পড়েছে। যে কারণে নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি গ্রাহকদের আস্থায় কিছুটা চিড় ধরেছে। এসব কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমানত কমেছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে উলেখ করা হয়েছে।
এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মুস্তফা কে মুজেরি বলেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেয়াদি আমানত ছাড়া অন্য কোনো আমানত রাখা যায় না। ওখানে আমানত রাখতে গেলে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করতে হয়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে জাল-জালিয়াতির কারণে অনেক গ্রাহক টাকা ফেরত পাচ্ছেন না। এতে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থাহীনতা তৈরি করেছে। যে কারণে আমানত কমছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারি খাতের সঞ্চয়পত্রের সুদের হার বেশি। এ কারণে সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে ঋণ নিলে সরকারকে বেশি সুদ দিতে হয়। এতে সরকারের খরচ বেড়ে যায়। এ কারণে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে সরকার বিনিয়োগ নীতিমালা কঠোর করেছে। একই সঙ্গে পণ্য ও সেবার মূল্য বাড়ায় এবং আয় কমায় মানুষের ক্রয় করার সক্ষমতাও কমেছে। এসব মিলে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ অর্ধেক কমে গেছে। জাতীয় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগের স্থিতি মে পর্র্যন্ত ৩ লাখ ৪০৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রি ছিল ৩৭ হাজার ৩৮৬ কোটি টাকা। সদ্য বিদায়ি অর্থবছরের একই সময়ে নিট বিক্রি হয়েছে ১৮ হাজার ১৫৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমেছে ৫৫ শতাংশ। অর্ধেকের বেশি কমে গেছে।
এদিকে গত বছরের মে মাসের তুলনায় চলতি বছরের একই মাসে নিট বিক্রি কমেছে ৪ গুণের বেশি। গত বছরের মে মাসে নিট সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছিল ২ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা। মে মাসে তা কমে বিক্রি দাঁড়িয়েছে ৬৩৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ ওই সময়ের ব্যবধানে সঞ্চয়পত্রের নিট বিক্রি কমেছে ৪ গুণের বেশি।
করোনার আগে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সঞ্চয় বেড়েছিল। কিন্তু করোনার পর সঞ্চয় কমতে শুরু করেছে। কেননা করোনার সময়ে অনেকে সঞ্চয় তুলে দৈনন্দিন খরচ নির্বাহ করেছেন। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ২০২০ সালে সঞ্চয় বেড়েছিল ২২ শতাংশ। গত বছরে বেড়েছে ১৬ শতাংশ।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে গত বছরের মে মাসের তুলনায় চলতি বছরের মে মাসে (পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে) মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। অনেকে মনে করেন প্রকৃত মূল্যস্ফীতির হার ১২ শতাংশের বেশি। ব্যাংকে মেয়াদি আমানতের বিপরীতে সুদ দেওয়া হয় ৬ থেকে ৭ শতাংশ। যা মূল্যস্ফীতির চেয়ে কম।
এছাড়া আমানত ভেঙে নেওয়ার সময় ব্যাংকের নানা ধরনের ফি, সরকারের কর বাদ দিলে মূল টাকা আরও কমে যায়। এতে ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে বাড়ার পরিবর্তে আরও কমে যায়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুদের হার বেশি হলেও ওখানে ফেরত পাওয়া নিয়ে আছে নানা ঝুঁকি। এছাড়া সরকারের কর, প্রতিষ্ঠানে ফি ও মূল্যস্ফীতির হার সমন্বয় করলে প্রাপ্ত অর্থ নেতিবাচক হয়ে যায়।
ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুনাফার হার খুবই কম। অনেক ক্ষেত্রে তা ৫ থেকে ৬ শতাংশের মধ্যে। সরকারি খাতের সঞ্চয়পত্রগুলোতে ভালো মুনাফা পাওয়া গেলেও এগুলো সবার পক্ষে কেনা সম্ভব হয় না কঠোর বিধিনিষেধের কারণে। এছাড়া প্রার্ন্তিক মানুষের পক্ষে তা কেনা সম্ভবও নয়।