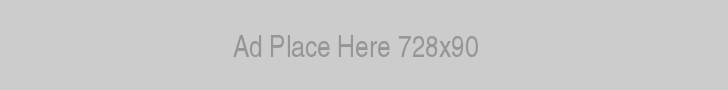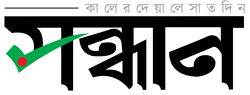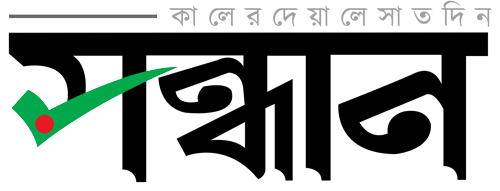সুধীর সাহা : আমেরিকার এক নদীর গল্প। ১৯০০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি পাশের কলোরাডো নদী থেকে খালের মাধ্যমে স্যালটন সিংকের পানি নিয়ে আসার কাজ শুরু করে। ১৯০৫ সাল নাগাদ এ খাল কাটার কাজ সম্পন্ন হয়। কলোরাডো নদী থেকে পানির স্রোত বইতে শুরু করে শুষ্ক স্যালটন সিংকে। শুষ্ক ডোবা ভরে ওঠে নদীর পানিতে। তখন থেকেই এটি প্রাণবন্ত হ্রদে পরিণত হয়। এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করা লোকজন সেই পানি কাজে লাগিয়ে চাষাবাদ শুরু করে দেয়। কিন্তু দু’বছরের মধ্যেই নদী আর হ্রদের সংযোগকারী খালে পানি জমে এর নাব্য কমে আসে। বন্যা দেখা দেয় এবং কলোরাডো নদীতে বান আসে।
নদীর পানি স্যালটন হ্রদ ছাড়াও আশপাশের উপত্যকা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই বিশাল পানি জমেই তৈরি হয়ে যায় স্যালটন নদী। খুব অল্প সময়েই ক্যালিফোর্নিয়ার কলোরাডো মরুভূমির প্রাণ হয়ে ওঠে এই স্যালটন নদী। বছরের অন্যান্য সময় পানি শুকিয়ে গেলেও প্রতি বছর বর্ষায় পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ নদী। এ নদীকে কেন্দ্র চাষাবাদ এবং পর্যটনের প্রসার ঘটতে শুরু করে; প্রচুর বণ্যপ্রাণীর দেখা মিলতে শুরু করে। নদীর পানি মাছ চাষের কাজে লাগে এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছের দেখা মিলতে শুরু করে। অন্যদিকে, মাছের খোঁজে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে অস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য নানা ধরনের পাখিরাও উড়ে আসতে থাকে। সারাদিন পাখির ডাক আর নদীর জলের কলতানে প্রাণোচ্ছ্বল হয়ে থাকত স্যালটন নদী।
বর্ষার পানিতে পুষ্ট এ নদীতে প্রতি বছর কলোরাডো নদী থেকে পানি আসত। সারা বছর এ পানি থাকত স্যালটন নদীর বুকে। কিন্তু বর্ষার সময় পানি উপচে পড়ে নদীর দু’কূল ভাসিয়ে নিতে থাকে। প্রতি বছরের এ বন্যা রুখতে কলোরাডো নদীতে বাঁধ তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় ক্যালিফোর্নিয়া প্রশাসন। ১৯৩৮ সালে কলোরাডো নদীর ওপর বাঁধ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়। বাঁধটির নাম দেওয়া হয় ‘ইম্পিরিয়াল বাঁধ’। এ বাঁধ দিয়েই বন্যা রুখে দেয় প্রশাসন। মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ফলে ওই অঞ্চলে ব্যবসার নতুন মাত্রা যোগ হয়। স্কুল, ক্লাব, হোটেল গজিয়ে উঠতে শুরু করে নতুন করে। কিন্তু বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় না।
বাঁধ নির্মাণের পর মানুষ বন্যার হাত থেকে বাঁচলেও নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে থাকে কয়েক বছর পর থেকে। বাস্তব ফল হয় মারাত্মক। স্যালটন নদীতে বর্ষার পানি আসা বন্ধ হয়ে যায়। স্যালটন নদীতে জমে থাকা পানি বাষ্প হয়ে শুকাতে শুরু করে। যে পরিমাণ পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তার সমপরিমাণ পানি নতুন করে ঢুকছিল না। ফলে স্যালটন নদীতে পানির পরিমাণ ক্রমেই কমে আসতে থাকে। ১৯৭০ সালেই সেখানকার পরিবেশবিদরা প্রশাসনকে সতর্ক করেছিলেন। নদীর প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে বলে সতর্ক করেছিলেন। কিন্তু তাতে কান দেয়নি ক্যালিফোর্নিয়া প্রশাসন।
স্যালটন নদীর সেই সুদিন আজ আর নেই। তার পানি এতটাই বিষাক্ত হয়ে গেছে, তাতে না খেলা করে মাছেরা; না উড়ে এসে সাঁতার কাটে কোনো পাখি। নদীর মাছ মারা যেতে থাকে। নদীর পানি শুকিয়ে গিয়ে অত্যন্ত লবণাক্ত হয়ে ওঠে। সেখানে কোনো প্রাণীর পক্ষে টিকে থাকা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। ওই পানি দিয়ে আর চাষাবাদেও সাহায্য করা সম্ভব হলো না। পানিতে মরা প্রাণী পচন ধরে যেতে শুরু করে। একদিকে নদীর পানি সম্পূর্ণ শুকিয়ে আসে, আর অন্যদিকে মৃত প্রাণীদের দেহ পচে বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়। ক্রমেই নদীকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া বসতিও অন্যত্র সরে যেতে শুরু করে।
সেখানে বায়ুদূষণ এতই প্রবল ও মারাত্মক যে, তার বিষাক্ত গ্যাস লস অ্যাঞ্জেল্স পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। একসময় যে স্যালটন নদী ক্যালিফোর্নিয়ার কলোরাডো মরুভূমির প্রাণ হয়ে উঠেছিল, আজ তা বায়ুদূষণের সবচেয়ে বড় কারণে রূপ নিয়েছে। এ গভীর সংকট সমাধানে এগিয়ে এসেছে আমেরিকার প্রশাসন, বিজ্ঞানী আর পরিবেশবাদীরা। গবেষণা হচ্ছে, কীভাবে শিগ্গির বাঁচা যায় এ বায়ুদূষণ থেকে।
আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ঢাকা। স্যালটন থেকে ইছামতি নদী। কতটা ব্যবধান? হয়তো অনেক। কারণ ওটা আমেরিকা। ওখানে যেমন লাভের আগেও গবেষণা হয়, ক্ষতির আগেও তেমনি গবেষণা হয়। বাংলাদেশের গবেষণা শব্দটিই যেন গতি হারিয়ে বসে আছে। জনগণের লাভ হচ্ছে কিনা, ক্ষতি হচ্ছে কিনা, তা যেন এখানে গবেষণার বস্তু নয়। তা নিয়ে ভাবতে যেন প্রশাসন তাদের বড় বড় কাজ থেকে মাথাটা ঘুরাতে নারাজ। কিন্তু তারপরও এক জায়গায় মিল আছে। মিল দেখতে পাচ্ছি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার স্যালটন নদী আর বাংলাদেশের নবাবগঞ্জ-কেরানীগঞ্জের ইছামতি নদীর মধ্যে।
ইছামতি নদী মানিকগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দোহার, কেরানীগঞ্জ এই বিশাল এলাকার প্রায় দশ লাখ মানুষের অন্যতম আশা-ভরসার জায়গা ছিল একসময়। স্থলপথের পাশাপাশি রাজধানী ঢাকার সঙ্গে এ ইছামতি নদীই স্থাপন করে রাখত একটি নৌপথ। নৌকা চলত, লঞ্চ চলত। মাছ খেলা করত। পাখিরা কলরব করে কখনো পানিতে, কখনো পাড়ের গাছে খেলা করত। চাষি চাষাবাদের স্বার্থে ইছামতি নদীর পানি সেচকাজে ব্যবহার করত। এ অঞ্চলের মাছ ব্যবসায়ীরা ইছামতি নদীকে ঘিরেই জীবিকা নির্বাহ করত।
একসময় বর্ষা মৌসুমে পদ্মার পানি ঢুকে যেতে থাকে ইছামতির বুকে। সেই পানির স্রোতে ইছামতির দু’কূল ভেসে যায়। নিরাপত্তার অভাব অনুভব করে ইছামতির দু’পাড়ের মানুষ। বন্যার হাত থেকে বাঁচার আর্তচিৎকার ওঠে। সরকার এগিয়ে আসে, প্রশাসন এগিয়ে আসে। স্থানীয় সমাজসেবকরাও এগিয়ে আসেন। পরিস্থিতির সামাল দেওয়া হয় জয়কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের শেষ মাথায় বেড়িবাঁধ নির্মাণ করে। বর্ষায় পদ্মার পানি আর আসতে পারে না। বাঁধ দিয়ে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবার শুরু হয় নতুন ব্যবসায় জায়গা। ইছামতির দু’পাড়ের মানুষ রক্ষা পায় প্রতি বছরের বন্যার হাত থেকে। বেড়িবাঁধে গড়ে ওঠে নতুন দোকান, রেস্তোরাঁসহ নানা ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।
কিন্তু শুরু হয় আবার অন্য গল্প। সেই স্যালটন নদীর গল্প। ইছামতি নদীতে আর পদ্মার পানি আসতে পারে না। ইছামতি নদীতে জমে থাকা পানি বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়ে নদীকে শুকনো করে ফেলে। বর্ষায় কিছুটা পানি দেখলেও শুষ্ক সময়ে দেখা দেয় পানিশূন্যতা। মাছ আর দেখা যায় না। সেচ কাজে আর পানি পাওয়া যায় না। নদীতে আর পাখিরা আসে না। নদীর দু’পাড় ধীরে ধীরে ভরে যেতে থাকে আবর্জনায়। দু’পাশের কিছু মানুষ আবর্জনা ফেলে ফেলে ভরে ফেলে ইছামতির খানিকটা জায়গা। একদল দখল করতে থাকে পাড়ের জায়গা। নদীর পানিতে দেখা দেয় বিষাক্ত গ্যাসের সম্ভার। সেই পানিতে মরে থাকতে দেখা যায় মাছ, প্রাণী, পাখি। পরিবেশদূষণের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায় একসময়ের প্রাণচঞ্চল ইছামতি নদী।
এখানেও পরিবেশবাদীরা আওয়াজ তোলেন, প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাঁধ নির্মাণের সময় যে বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, সেই স্লুইচগেট করার তাগাদা দেন। সরকারের কাছে ধরনা দেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দুয়ারে দুয়ারে যেতে থাকেন। কিন্তু শোনে না প্রায় কেউ-ই। একে তো এটি একটি নদীর বিষয়। তাতে বেশি দৃষ্টি দেওয়ার সময় কোথায়? কিইবা রাজনীতি আছে এখানে? তাই এড়িয়ে যাওয়ারই স্রোত বেশি। ইছামতি নদীর স্রোত থেকে তো সেই স্রোতের গতি অবশ্যই বেশি। তাই এখনো ইছামতি শুধু ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। এ অঞ্চলে তো সবাই আছেন! প্রশাসন আছে, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ আছে, জনপ্রতিনিধি আছেন। কিন্তু তাদের ততটা সময় নেই পরিবেশ নিয়ে ভাবার, ইছামতি নদীকে নিয়ে ভাবার। পরিবেশবাদীরা দৌড়ে দৌড়ে বিভিন্ন মহলে যাওয়ার চেষ্টা করলেও দোষ হয়ে যায় অনেক সময়ে। কী স্বার্থ তাদের? তারা কেন এসবের মধ্যে আসবে? জনপ্রতিনিধিদের লোকজন যেন তেড়ে আসেন। তাই দৌড়ে গিয়েও আবার পেছনে ফিরে তাকাতে হয়।
ইছামতি নদীতে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, সেই বেড়িবাঁধে স্লুইচগেট করতে পারলেই আজকের শুকিয়ে যাওয়া মৃত ইছামতি নদীকে হয়তো বাঁচানো যেত। তাহলে পানি আসত যখন যা প্রয়োজন, সেই হিসাবে। পদ্মা তখন ইছামতির দু’কূল ভাসাতেও পারত না, আবার শুকিয়ে যেতে সাহায্যও করতে পারত না। কিন্তু সেই স্লুইচগেটটি তো সরকার করবে! তারা জানে এবং বুঝে-ইছামতিকে বাঁচানো প্রয়োজন। কিন্তু শেষ রক্ষাটি হয়ে উঠছে না। যাদের দেখার প্রয়োজন, তাদের দৃষ্টি অন্য জায়গায় কাজ করে। নদীতে মাছ আছে, পানি আছে, সেচ-সাহায্য আছে, পাখির সুযোগ আছে, কিন্তু এগুলো তো পরিবেশের কথাবার্তা।
এগুলো দিয়ে করপোরেট দুনিয়ায় কি কোনো কিছু করা যায়? তাইতো এ নদীতে শুধু পরিবেশবাদীদের চিন্তার জায়গা আছে, গরিব জেলেদের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা আছে, গরিব কৃষকের সেচ সুবিধা আছে, পাখিদের গান গাওয়ার সুযোগ আছে। তাই চিন্তাটাও তাদেরই। কিন্তু সেখানেও তো বিপদ আছে। গরিবের পক্ষে কেউ এগিয়ে এলে তো আবার তা-ও পছন্দের নয় কর্তৃপক্ষের। নিজেরা করবে না, আবার কাউকে করতেও দেবে না! তাহলে সমস্যা সমাধান হবে কী করে?
স্যালটন নদীর সমস্যা নিয়ে আমেরিকার গবেষণা জগৎ আজ তোলপাড়। প্রশাসন দিনরাত কাজ করছে, কীভাবে এ সমস্যা থেকে ওই অঞ্চলকে রক্ষা করবে তা নিয়ে। ঠিক বিপরীত চিত্র বাংলাদেশের ইছামতি নদীর ক্ষেত্রে। এখানে গবেষণা নেই, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই। নদীর শুষ্কতায় পরিবেশের কী ক্ষতি হচ্ছে, কতখানি দূষণ ছড়াচ্ছে মরা নদী-তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। তবে এসব নিয়ে বেশি লেখালেখি করলে সেসব বাড়াবাড়ি থামিয়ে দিতে কর্তৃপক্ষের অভাব নেই। আগে ভাবতাম, পরিবেশ নিয়ে কথা শুরু হলেই মনে হয় বেশ একটা সর্বজনপ্রিয় সর্বসম্মত শুভ চিন্তার অঙ্গনে প্রবেশ করা গেল।
সবাই চাই সুন্দর পৃথিবী, সবুজ অরণ্য, নির্মল নদীর পানি, নীল আকাশ, দূষণহীন পরিবেশ। টিভিতে, কাগজে, হরেকরকম এনজিওর প্রচারপত্রে ‘পরিবেশ বাঁচাও’-এর পবিত্র আহ্বান। কিন্তু এমন এক প্রেক্ষাপটেও অনেকেই পরিবেশ নিয়ে কথা বলাকে বাহুল্য মনে করে। এক ধরনের মানুষ আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার দানে উন্নত জীবনযাপন করে এবং ভাবেসাবে পরিবেশপ্রেমী বা পরিবেশবিলাসী হয়ে ওঠে। প্রগতিশীল আবেগের ফুলঝুরির আড়ালে উন্নয়ন সহায়ক করপোরেট দুনিয়ার চিন্তাই তাদের মাথায় থাকে সবসময়।
সুধীর সাহা : কলাম লেখক