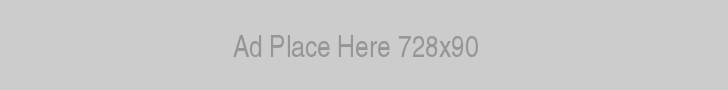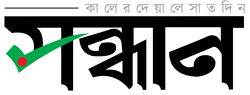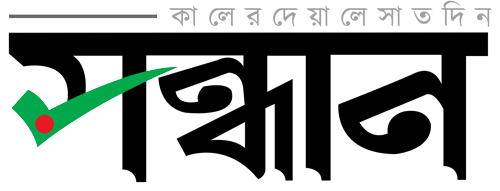বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়াকে অর্থনৈতিক সক্ষমতার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এখনই সতর্ক পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন বিশ্লেষকেরা। তারা বলছেন, রিজার্ভ কমে যাওয়া মানে হচ্ছে অর্থনেতিক সক্ষমতা কমে যাওয়া।
আর তারা পরিস্থিতি সামলাতে কমপক্ষে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ঋণ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আইএমএফ থেকে।
সর্বশেষ রপ্তানি ব্যয় পরিশোধের পর বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আছে ৩৯ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন মর্কিন ডলার। গত সপ্তাহে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নকে (এসিইউ) ১ দশমিক ৯৯ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় নিষ্পত্তির পর রিজার্ভের এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। গত ডিসেম্বরে রিজার্ভ ছিল ৪৬ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার।
গত দুই বছরের মধ্যে এই প্রথম রিজার্ভের পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেল। ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশের রিজার্ভ ধারাবাহিকভাবে বাড়তে থাকে। ওই বছরের জুন মাসের শেষে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৫ দশমিক ৩২ বিলিয়ন ডলার। গত বছরে আগস্টে প্রথমবারের মতো রিজার্ভের পরিমাণ ৪৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার হয়। এরপর কমতে থাকে। গত অর্থবছরের শেষ দিন ৩০ জুন রিজার্ভ ছিল ৪১ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলার।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়া, সেই অনুপাতে রপ্তানি না বাড়া, রেমিট্যান্স কমে যাওয়া এবং ডলারের তুলনায় টাকার অবমূল্যায়ন রিজার্ভ কমে যাওয়ার প্রধান কারণ। আর জ্বালানি আমদানিতে ব্যয় আরও বেড়ে গেলে রিজার্ভে টান বাড়তেই থাকবে। সাধারণভাবে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো রিজার্ভ থাকার কথা বলা হলেও রিজার্ভ কমে যাওয়া অর্থনৈতিক শক্তি কমে যাওয়াকে ইঙ্গিত করে। বাংলাদেশের এখনও পাঁচ-ছয় মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর মতো রিজার্ভ থাকলেও তাতে আশ্বস্ত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, আমদানি ব্যয়ের তুলনায় রপ্তানি আয় কমতে থাকলে রিজার্ভও কমতে থাকবে। একই সঙ্গে প্রবাসী আয় কমতে থাকলেও পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে পারে। বাংলাদেশকে গড়ে মাসে এখন সাত মিলিয়ন ডলারের বেশি আমদানি ব্যয় মেটাতে হয়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা বলব না যে আমরা একেবারে সংকটের মধ্যে আছি। ৪০ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি রিজার্ভ মানে হচ্ছে ছয় মাসের মতো রপ্তানি ব্যয় মেটানো যাবে। তিন-চার মাসের থাকলেই চলে। তবে এখানে আশঙ্কার বিষয় হলো রিজার্ভ দ্রুত কমে গেছে অল্প সময়ের মধ্যে।
বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় বেড়ে গেছে। গত অর্থবছরের জুলাই থেকে মে, ১১ মাসে আমদানি হয়েছে ৭৫ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের। যা আগের তুলনায় ৩৯ শতাংশ বেশি। এই সময়ে রপ্তানিও বেড়েছে কিন্তু আমদানির তুলনায় কম। ৪৪ দশমিক ৪২ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি হয়েছে। বেড়েছে ৩৩ শতাংশ। বাংলাদেশে এই প্রথমবারে মতো প্রবাসী আয় কমেছে। গত অর্থবছরে রেমিটেন্স এসেছে দুই হাজার ১০৩ কোটি ডলার। আর তার আগের অর্থবছরে রেমিটেন্স আসে দুই হাজার ৪৭৭ কোটি ডলার।
ড. সালেহউদ্দিন মনে করেন, এখন যে রিজার্ভের হিসাব দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) আছে। এটা তো রিজার্ভ থেকেই দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে সাত বিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়ে গেছে। সেটা কি ফেরত এসেছে? না আসলে সেই ডলার তো আর রিজার্ভে নেই।
আরও একটি সমস্যা হলো টাকার অবমূল্যায়ন হওয়ায় পেমেন্ট রেট আরও বেড়ে যাবে বলে জানান তিনি।
সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম মনে করেন, আশঙ্কার বিষয় না থাকলেও দ্রুতই রিজার্ভ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। আমদানি কমাতে হবে। বিশেষ করে বিলাসবহুল পণ্যের। সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। এলসি মার্জিন বাড়িয়েছে। কিন্তু সেটা কতটা কার্যকর হচ্ছে দেখা দরকার। রপ্তানি বাড়াতে হবে। আর রেমিট্যান্স বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। প্রণোদনা বাড়ানো যেতে পারে। কার্ব মার্কেটে তো ডলারের দাম ব্যাংকের চেয়ে বেশি। তাই সব রেমিট্যান্স ব্যাংকিং চ্যানেলে আনার ব্যবস্থা করতে হবে।
সিপিডির গবেষণা পরিচালক অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন, এখনও পাঁচ-ছয় মাসের আমদানি ব্যয় পরিশোধের রিজার্ভ আছে, সেটা ভেবে আশ্বস্ত হওয়া যাবে না। কারণ, দ্রুত রিজার্ভ কমে যাওয়া অর্থনীতির সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। রিজার্ভ বেশি থাকলে অর্থনীতি স্থিতিশীল থাকে। এক সময়ে আমাদের আট মাসের মতো আমদানি ব্যয় পরিশোধের সক্ষমতা ছিল।
তিনি বলেন, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা আসার খাতগুলোর যদি অগ্রগতি না হয়, তাহলে আমাদের দেশের বাইরের আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে হবে। বিশ্বব্যাংক ইতোমধ্যে এক বিলিয়ন ডলার দেওয়ার কথা বলেছে। সরকার আইএমএফ থেকে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের ঋণ নেওয়ার আলোচনা শুরু করেছে। তবে এই উদ্যোগগুলো আরও আগে নেওয়া দরকার ছিল।
অব্যাহতভাবে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি এবং বিদ্যুতের জন্য মিক্সড ফুয়েল এখন রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। আর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো সঠিক পরিকল্পনা না করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন তিনি।
বাংলাদেশ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পে ১৪০ বিলিয়ন ডলারে ঋণ নিয়েছে। ২০২৩ সাল থেকে ঋণ পরিশোধ শুরু করতে হবে। আর সুদ পরিশোধের পরিমাণও বাড়ছে। শুধু রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পেই ২০২৩ সাল থেকে বছরে ৫৬৫ মিলিয়ন ডলার সুদ দিতে হবে।
সিপিডির বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য মনে করেন, ঋণ ও সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে ২০২৩-২৪ সাল থেকে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে। রিজার্ভের ওপর তখন আরও অনেক বেশি চাপ পড়বে।
তিনি বলেন, আমদানি-রপ্তানির ভারসাম্য এবং রেমিট্যান্স এই দুই জায়গায়ই আমরা স্মরণকালের সবচেয়ে বড় ঘাটতিতে আছি। আর আমারে রেকর্ড রপ্তানি মূলত আমদানিনির্ভর রপ্তানি। রেমিট্যান্সের যাদুও শেষ হয়ে যাবে। রেমিট্যান্স বাড়বে আবার কমবে। কিন্তু অব্যাহতভাবে বাড়ার ট্রেন্ড থাকবে না। তাই আমাদের এখন রিজার্ভ ঠিক রাখতে উদ্যোগ প্রয়োজন। বড় ধরনের বৈদেশিক বিনিয়োগ আসলে আমাদের সক্ষমতা বাড়ত। কিন্তু সেটাতো দুই বিলিয়ন ডলারের বেশি হয় না। একমাত্র ইতিবাচক জায়গা হলো বৈদেশিক সাহায্য। গত বছর আট বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য না আসলে পরিস্থিতি অনেক খারাপ হতো। এটাই আমাদের রিজার্ভ এবং টাকার মানকে এখনো টিকিয়ে রেখেছে। সরকার আগেই আইএমএফ-এর কাছে গেলে ভালো হতো। আইএমফ আর্থিক ব্যবস্থাপনার কিছু শর্ত দেবে। তাই দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনাই আগামীর মূল চ্যালেঞ্জ।
সৌজন্যে : ডয়েচে ভেলে